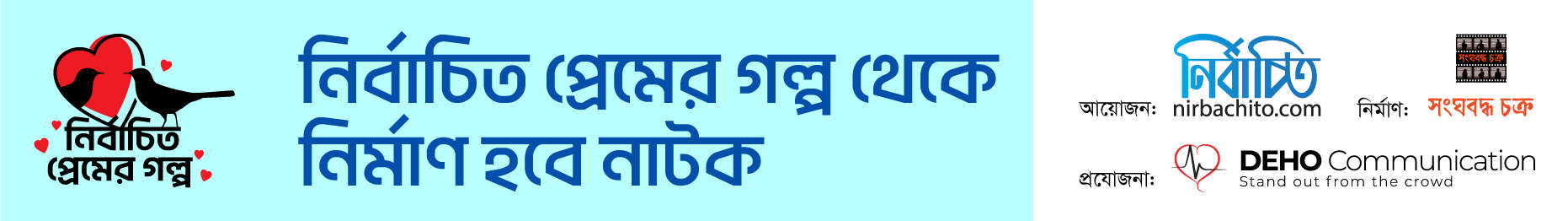বর্ষা এলে সবচেয়ে বেশি বিরক্ত হতো মা। আকাশ গলে বৃষ্টির ফোঁটা মাটিতে পড়ার আগেই মা’র বিরক্তিমাখা দৃষ্টি গিয়ে পড়তো আব্বার ওপর। এই লোকটা যদি একটু কাজের হতো। আজ করি, কাল করি করে করে এখনো রান্নাঘরের চালাটা ঠিক করে দিলো না। বর্ষা তো নেমে গেল প্রায়। এখন কী হবে। কী করে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে রান্না করে খাওয়াবে। বৃষ্টির পানি দুই ফোঁটা যদি বাইরে পড়ে, তিন ফোঁটাই পড়ে তার রান্নাঘরে। আসন্ন বর্ষা ও বর্ষাজনিত সমূহ বিরক্তিকর পরিস্থিতির আশঙ্কায় আব্বার সাথে গজগজ করে দিন পার করেন মা। আর আব্বা যেন সর্বংসহা ঋষি-সন্ন্যাসী। মা’র শত ভর্ৎসনা সদ্য ডুবোজল থেকে উঠে আসা হাঁসের মতো গা ঝাড়া দিয়ে ঝেড়ে ফেলেন। তার মুখের হাসি মিলায় না। দিনের পর দিন মাকে আশ্বস্ত করে চলেন, চিন্তার কিছু নেই। বর্ষার আগেই ঠিক হবে চালা।
তারপর একদিন মা’র আশঙ্কাই সত্য হয়। রান্নার চালা ঠিক করা হয় না, অথচ চারিদিক অন্ধকার করে, সূর্যের আলো নিভিয়ে দিয়ে, গুমোট ঘুমসে গরম ভেদ করে কাঁঠাল, নারিকেল, তাল-সুপারি, শজনে গাছের ডালপালার ফাঁক গলে নেমে আসে পয়লা আষাঢ়ের বৃষ্টি। উঠোনে শুকোতে দেওয়া মুড়ি ভাজার ধান, ছাপড়ার চালে কুলোয় করে বিছিয়ে দেওয়া আমচুর, বাড়ির আঙিনার শুকনো খড়ি-লাকড়ি বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য লেগে যায় হুটোপুটি।
একদিন, দু’দিন, তিনদিন। ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে বৃষ্টির স্থায়িত্ব। কখনো কখনো টানা চার পাঁচদিনে সূর্যের মুখদর্শন হয় না। দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা পিনপিনে বৃষ্টি। টানা বৃষ্টিতে বাড়ির উঠোনের মাটি ভিজে জমে থাকে মোমের মতো। পা দিলেই পিচিক করে ঢুকে যায় গোড়ালি অবধি। একটু শক্ত যেখানে মাটির বুনোট, সেখানে জমে সবুজাভ শ্যাওলা। এই পর্বে মা’র জন্য দরদি হতে দেখা যায় আব্বাকে। পাছে আবার রান্না করে ঘরে ফেরার সময় পা পিছলে পড়ে যায় মা, এই আশঙ্কায় উঠোনের বুকে ধাপে ধাপে একটা বা দু’টো করে ইট বিছিয়ে দেন আব্বা শোয়ার ঘর থেকে রান্নাঘর বরাবর। মা এতে খুশি বা বেজার কিছুই হন না। মাথার ওপর গামছা বা পুরনো লুঙ্গির কাপড় ফেলে বৃষ্টিজলের ছাঁটের সাথে পাল্লা দিয়ে ভিজেপুড়ে রান্না করেন তিনি। দেখতে দেখতে উঠোনে বিছিয়ে দেওয়া ইট আলগোছে ঢুকে যায় নরম মাটির বুকে। চারপাশ থেকে নরম কাদামাটি ইটগুলোকে গলা পর্যন্ত চেপে ধরে। সেই ইটের ওপর সাবধানী পা ফেলে কড়াইয়ের দুই হাতলের মধ্যে খুন্তি ঠেলে দিয়ে এক হাতে তরকারির কড়াই আর অন্য হাতে পেঁয়াজ-মরিচের ডালা নিয়ে মা উঠে আসেন ঘরে।
টানা বর্ষণকে মা বলতেন ‘কাইত্তান’। আব্বার সাথে গজগজ করতে করতে বলতেন, মরার কাইত্তান তো নামছে। থামার কোনো নাম গন্ধ নেই। এইবার খাইয়ো পেট ভরে গরম গরম ভাত। আমি পারব না। আমি পারব না এমন রোজ রোজ বৃষ্টিতে ভিজে তোমাদের রান্না করে খাওয়াতে। কতবার বলছি রান্নাঘরটা ঠিক করে দাও। আমার কথা গায়েই লাগালে না। কাল থেকে আর রান্নাবান্না নাই। মুড়ি খেয়ে থাকবা সকলে।
মা’র এমন নিস্ফলা ভর্ৎসনায় আব্বা বোধহয় কৌতুকবোধ করেন। উঠোনে প্যাঁকপ্যাঁক করে হাঁটতে থাকা রাজহাঁসের বাচ্চাগুলোর দিকে তাকিয়ে কণ্ঠে রস ফুটিয়ে বলেন, বৃষ্টির দিনে মুড়ি খাইতে খারাপ না। ঝাল লবণ একটু বেশি করে সরিষার তেল দিয়া মাখলে মুড়ি তো বেহেশতি খাবার।
আব্বার কথায় ঈষাণ কোণে যেন প্রবল বেগে বাজ পড়ে, বিদ্যুৎ চমকায়। দারুণ রোষে হুড়মুড় করে নেমে আসে ঢল। ডালের পাতিলে হঠাৎ উড়ে এসে পড়া রেইন্ট্রি কড়ই পাতা উড়োং দিয়ে তুলতে তুলতে মা বলেন, আমি তো দাসিবান্দি। তোমরা বাপ বেটারা তো সব জমিদারের বংশধর। আমি ভিজলে তোমাদের কী। কিছুক্ষণ পর আব্বাকে দেখা যায় সারের বস্তা, পলিথিন কেটেকুটে জোড়াতালি দিচ্ছেন রান্নাঘরের চালা। সেদিকে মা’র বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। কলপাড়ে গোসল করে ভেজা কাপড় তিনি ঘরের বারান্দায় টানানো দড়িতে মেলে দেন। কায়দা করে গামছায় মুড়িয়ে রাখেন দিগন্ত কালো আকাশের মতো মিশমিশে ঘনচুল। কী যে স্নিগ্ধ, কোমল আর মায়াময় লাগে মাকে তখন। তারপর মেঝেতে পাটি পেতে খেতে দেন আমাদেরকে।
দ্বিতীয় দফা বৃষ্টি নামলে সারের বস্তা দিয়ে বানানো বিশেষ লম্বা টুপি মাথায় পরে জাল খুটি নিয়ে বের হন আব্বা। আব্বার সাথে সাথে ছাতি মাথায় হাতে একটা পাতিল নিয়ে লুঙ্গি কাছা মেরে বড়ালের পাড়ে যাই আমরা। ক’দিন আগেই যে বড়াল ছিল সরু নালার মতো, রুগ্ন, মৃতপ্রায় ছিল যার শ্যাওলাজলের ধারা, টানা বর্ষণে সে ফিরে পেয়েছে যেন হারানো যৌবন। ঘোলাটে চোখে তারুণ্যে ভরা টগবগে দেহ নিয়ে ছুটে চলছে সে পশ্চিম থেকে পূর্ব দকককে। কী তার জলের তেজ, কী তার ঢেউয়ের গর্জন। নদীর ধারে পৌঁছে দেখা গেল আমরাই বোধহয় পিছিয়ে পড়ার দল। দুপুরের আগ থেকেই অনেকে নেমে গেছে মাছ ধরতে।
তখন আমি ভাবতাম, বর্ষায় নতুন মেঘের পানির সাথে নিশ্চয়ই আকাশ থেকে মাছ পড়ে। যদি না পড়ে, তাহলে এত মাছ আসে কোত্থেকে? এই তো ক’দিন আগেই সব ছিল শুকনো ঠনঠনাঠন। সামান্য কিছু পানি যেখানে জমেছিল, সেগুলো ছিল সব ব্যাং আর ব্যাঙাচিদের অভয়াশ্রম। দু’তিন দিনের বৃষ্টিতেই এত মাছ কোত্থেকে হলো? আব্বা একেকবার জাল টানেন, আর জালের ওপর তিড়িংবিড়িং করে লাফাতে দেখা যায় বউপুঁটি। কী তার রঙ, কী তার রূপ। লেজ থেকে মাথা বরাবর পেটের ওপর দিয়ে গাঢ় কমলা রঙের ডোরা। একেবারে যেন চকচক করছে গা। দেখতে দেখতে আমার পায়ের কাছে থাকা পাতিল ভরে ওঠে বউপুঁটি, বেলে, টেংরা, ছোটো বাইম, কাঁটাবাতাসী, মলা ঢেলা মাছে।
বিকেল পড়ে আসে। ভাতের বড়ো পাতিলটার গলাগলা ভরে তরতরে তাজা মাছ নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসি আমরা। পাতিলের ভেতর ভেসে থাকে মুক্তো দানার মতো মাছের বুদবুদ। বৃষ্টির জলে ভিজে একাকার আব্বা। সারের কাগজ যেটা মাথায় দিয়েছেন, তাতে মাথা বাঁচে কোনোরকমে, কিন্তু গা বাঁচে না। তাছাড়া মাছ ধরার তালে পড়লে গা ভিজলো কী মাথা ভিজলো সেই খেয়াল থাকে না। ছাতা হাতে থাকলেও বাড়িতে ফিরে দেখা গেল আমারও সারা গা ভেজা। আমরা ভেজা কাপড় ছাড়তে ছাড়তে মানকচুর পাতা বিছিয়ে মা বসে গেছেন বারান্দায় মাছ কুটতে। সন্ধ্যার আগে আগে টুকিটাকি সওদা কিনতে ছাতা মাথায় বাজারের দিকে বেরিয়ে যান আব্বা। আকাশ মেঘে ঢেকে থাকায় সূর্যমণি কখন অস্ত যায়, বোঝা যায় না। তবুও বৃষ্টিছাঁটের আড়াল গলে কেমন একটা আবছা আলো যেন ঠিকরে বেরোয়, গোধূলীর শেষ বিকেলের আলো। মাছ কুটতে কুটতে উঠোনে হেলে পড়া আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে মা আন্দাজ করেন, সূর্য ডুবে গেছে। গলা উঁচিয়ে বলেন, ঘরে সন্ধ্যা বাতিটা জ্বালা। মা’র আন্দাজ দেখে অবাক হই আমরা। আমি বা ভাইয়া কুপি বাতিতে আলো জ্বালার আগেই দূরের মসজিদ থেকে ভেসে আসা মাগরিবের আজান শুনতে পাই।
এদিকে বৃষ্টির যেন নিস্তার নেই কোনো। সন্ধ্যার পর যেন আরও পায় সে নতুন বেগ। মুষলধারে ঝরতে থাকে অনবরত। তুমুল বৃষ্টি উপেক্ষা করে রান্না ঘরের চালার নিচে যাওয়ার উপায় থাকে না। আব্বার খামখেয়ালিতে রান্নাঘরের চালা যে ঠিক হবে না এই বর্ষাতেও, মা তা আগেই জানতেন। সেজন্য চৈত্রমাসেই অনাগত বর্ষার আশঙ্কায় বানিয়ে রেখেছিলেন তিনি একটা আলোকচুলা। সেই চুলা এইক্ষণে বেরোয় চৌকির নিচ থেকে। শোবার ঘরের বারান্দায় আলোকচুলা পেতে শুকনো ঘুটে জ্বালিয়ে তাতে রান্না চড়ান মা। রাতের বেলা ধোয়াওঠা গরম ভাত আমরা খাই কড়কড়ে ভাজা পুঁটি, লাউ ডাঁটা দিয়ে কাঁটাবাতাসীর চচ্চড়ি আর কুমড়ো ফুলের বড়া দিয়ে।
রাত যায়, ভোর হয়, তবু বৃষ্টি থামে না। বাইরে বেরোনোর জো নেই, কাজেই গোয়ালেই বাঁধা থাকে গরু। ভেজা খড় চিবোয় সে আয়েশি ভঙ্গিমায়। বারান্দার বাঁশের খুঁটির সাথে ঝুলিয়ে রাখা কাঁঠাল পাতা, কলাপাতা খায় গাভীন ছাগল। উঠোনে কাদা মাটিতে মাথা বের করে দেওয়া কেঁচো ধরে খায় রাজহাঁসের বাচ্চাগুলো। আমরা বায়না ধরি কিছু একটা খাবার। রান্না হয়নি, অগত্যা শিমের বিচি, কাঁঠাল বিচি অথবা চাল ভাজা লেবু পাতা, পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে গুঁড়ো করে দেন মা। বাতাবি লেবুর পাতায় গড়া চামুচে করে আমরা আয়েশ করে খাই সেই চালভাজার গুঁড়ো। শিমের বিচি খোসা ছাড়িয়ে খাই কুটুরমুটুর। তারপর মা’র চোখ ফাঁকি দিয়ে কোনো এক ফাঁকে বেরিয়ে পড়ি ঘর থেকে। তারপর আর আমাদের পায় কে। সোজা নদীর পাড়, যেখানে আগে থেকেই পৌঁছে গেছে পাড়ার সমবয়সীরা। বর্ষাজলে ফুলেফেঁপেওঠা নদীর জলে আমাদের চলে দিনভর ঝাঁপাঝাপি। জলের ওপর হেলে পড়া হিজল ডালে চড়ে কে কত দূরে লাফিয়ে পড়তে পারে, চলে তার পাল্লা। এই তো ছিল আমাদের বর্ষাকাল তখন।
বাড়িতে একটিমাত্র লম্বা ডাঁটের ছাতা ছিল আমাদের। জরুরি কাজে যা নিয়ে বাইরে যান আব্বা। দাদা বাইরে যান বাঁশ-বেত-খড়ের তৈরি মাতলা মাথায়। আমরা না ভিজে বাইরে যেতে চাইলে মাথার ওপর কলাপাতা, মানকচু পাতা। শুধু আমাদেরই নয়, স্কুলের সময় গাঁয়ের পথে ঢল নামে মানকচু পাতা মাথায় স্কুলগামী ছেলেমেয়েদের। এক হাতে পলিথিনে জড়ানো বইখাতা বুকের সাথে চেপে ধরা সকলের। আর অন্য হাতে মাথার ওপর ছাতার মতো বিশাল আকৃতির মানকচু পাতা। স্কুলের জন্য বেরোনো হয় ঠিক, তবে সবদিন স্কুলে পৌছানো হয় না। তার আগেই পথে কোনো এক কদমগাছ দেখে বইখাতাগুলোর আশ্রয়মেলে মানকচুর পাতার নিচে। তারপর ছেলেমেয়েরা মেতে ওঠে বৃষ্টিভেজা কদমফুল নিয়ে। কদমের পাপড়ি খুলে বানানো হয় টেকো মাথার আব্দুল ঘটক, বর-কনে আরও সব বিচিত্র চরিত্র। পরিত্যক্ত ধানের খোলার শ্রমিকদের শেডের নিচে জড়ো হয়ে চলে চারগুট্টি, বাঘবন্দি, পাইট বা একিল-দেকিল খেলা। এই ছিল আমাদের বর্ষাকাল তখন। তখন আমরা ছোটো ছিলাম। তখন গ্রাম ছিল, চেনা মাটির ঘ্রাণ ছিল, বাঁশ, বেত, ঢোলকলমি, জলডুমুরের বন ছিল চারপাশে, পাড়ায় পাড়ায় পড়শি ছিল সকলে, আর আমাদের ছিল অদম্য শৈশব-কৈশোর। তখন আমরা ইশকুলের ছাত্র ছিলাম। তখন মানুষ ছিলাম। এখন আমাদের শিশুরা স্টুডেন্ট হয়ে গেছে! আর আমরা এখন হয়ে গিয়েছি নাগরিক!
রবিউল করিম মৃদুল