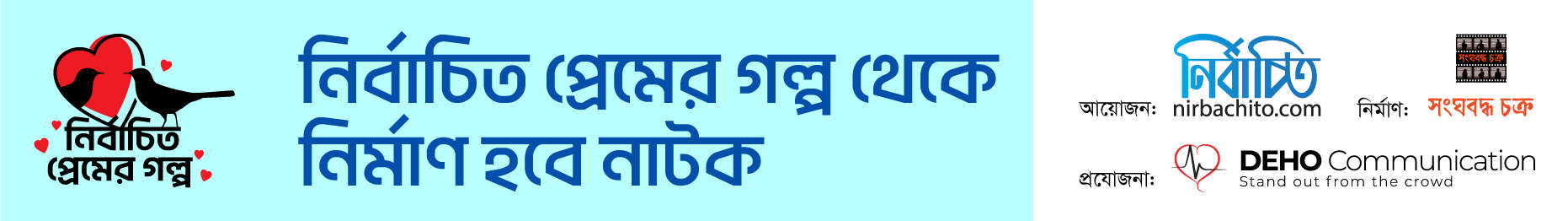১—
কোমরে দড়ি লাগিয়ে আমগাছের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে সীমাকে। একসময় পিঠে ছড়ানো গাঢ় অন্ধকারের মতো চুলগুলো এখন ছেলেদের চুলের মতো ছোটো ছোটো করে কাটা। সামনের দুটো দাঁত নেই। খুব মলিন পরনের কাপড়। হাড় জিরজিরে শীর্ণ শরীর। অথচ এক সময় ওর ঘনকালো চুলগুলোকে মনে হতো গহিন বন, টলটলে জলের দিঘির মতো ছিল গভীর দুটো চোখ। শ্যামলা রঙটা না হলে যেন কমতি হতো ওর সৌন্দর্যের। কী মায়াভরা একটা মুখ! কোনো কবির দৃষ্টিগোচর হলে অনায়াসেই লিখে ফেলতে পারতেন কয়েকটি পঙ্ক্তি। হরিণীর মতো উচ্ছ্বলা, চঞ্চলা সেই দুরন্ত কিশোরী সীমার এ কী হাল! তাকাতেই বুক ফেটে কান্না আসছিল। মাটির দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে একা একা কী যেন বলছে। যতটুকু শ্রুতিগোচর হলো তাতে মনে হলো ওর মায়ের সাথে কথা বলছে।
সীমা, সীমা বলে কয়েকবার ডাক দিলাম। কিছুতেই ফিরে তাকালো না। আপনমনে কথা বলেই যাচ্ছে। কতবার বললাম, সীমা, আমি এসেছি। তোকে নিয়ে যাবো আমার সাথে। এই যে দ্যাখ, তামিম তোকে ‘মা’ বলে ডাকছে।
তামিম সীমার একমাত্র ছেলে। অসুস্থতায়, অযত্নে ওর চেহারা এত খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে ছেলেটা ভয়ে কাছে যেত না। তাছাড়া, সীমা যখন ওকে রেখে পোশাক কারখানায় চাকরি করতে গিয়েছিল, তখন সারাক্ষণ নানার সাথে সাথে থাকতে থাকতে আপনজন বলতে সে নানাকেই চিনেছে। নানা-ই তার জগৎ। কতদিন সীমা আমার কাছে আক্ষেপ করেছে, ‘দ্যাখছো ফুপু, তামিম আমারে মা কইয়াও ডাকে না! অরে একটু মা ডাকতে কইয়া দিতে পারো?’
সীমা আর সীমার মা দুজনেই আমার মায়ের সাহায্যকারী ছিল। আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় হয় ওরা। সেই হিসেবে মাকে বুবু আর বাবাকে দাদা বলে ডাকত। ভিটেটুকু ছাড়া আর কোনো জায়গা জমি ছিল না ওদের। গায়ের শক্তিটুকুই ছিল দুবেলা দুমুঠো খাওয়ার মূল অবলম্বন। সংসারে একটু স্বচ্ছন্দ্যের জন্য ছোটোবেলা থেকেই বাবা-মায়ের সাথে সমান তালে ঘরে বাইরে কাজ করত সীমা। যখন খুব ছোট্ট, জামাও ধরেনি, তখন থেকেই ওর মায়ের সাথে কাজে আসত । সেই বয়স থেকেই একটা দুটো করে প্লেট ধুতো। তারপর শেলফে গুছিয়ে রেখে ওর মাকে কাজে সাহায্য করত। কাজ করত আর কুটুর কুটুর করে মা-মেয়ে গল্প করত।
একদিন বলতে শুনেছি—‘জানো মা, আমি মিথ্যা কথা একদম সত্য কথার মতো কইতে পারি।’
‘না রে মা, মিথ্যা কথা কওন ভাল না। কইলে মাইনষে তোরে আর বিশ্বাস করবো না। আমাগো ধর্মেও সত্যরে মিথ্যার লগে মিশান নিষেধ আছে।’
‘না না মা, পারলেও আমি কোনো সময় মিথ্যা কথা কইনা’।
সীমার ছোট্ট পৃথিবী ছিল ওর বাবা-মা, ভাইবোনকে ঘিরেই। অতটুকু বয়স থেকেই বাবা-মায়ের সাথে সংসারের ভালো-মন্দ চিন্তা ভাগ করে নিয়েছে। যে বয়সে পুতুল খেলার কথা, স্কুলে যাবার কথা সেই বয়স থেকেই সীমা চিনেছে এক ক্ষুধার্ত পৃথিবী। খেতে হলে লড়ে যেতে হবে। পুতুল বিয়ে দিয়ে কাঁদার সুযোগ হয়নি সীমার, মায়ের আঁচলের ছায়ায় থেকে খেলার ছলে শ্লেটে আঁকিবুঁকি করে বর্ণমালা শেখা হয়নি। শেখা হয়েছে– কীভাবে, কতটুকু শক্তি খরচ করলে থালাবাটি বেশি পরিষ্কার হয়, ভাগাভাগি করে অল্প খাবার খেয়েও কীভাবে পরিতৃপ্ত হতে হয়।
অনাহারে, অর্ধাহারে খেটে খাওয়া সীমার মা আসলে আর পেরে উঠছিল না। তাছাড়া, অ্যাজমা থাকায় মাঝে-মধ্যেই প্রচণ্ড শ্বাসকষ্টে মারা যাবার মতো অবস্থা হতো তার। সীমার জোরাজুরিতে কাজ ছেড়ে দিলো। তারপর থেকে সীমা নিজেই দুহাতে সামলে রাখত আমাদের। ভেতর থেকে ভালোবাসা ছিল আমাদের পরিবারের সবার জন্য। বিশেষ করে আমার আব্বা এবং মায়ের জন্য ওর শ্রদ্ধাবোধ, আদব-কায়দা ছিল লক্ষণীয়। কষ্টের কোনো কাজ মাকে করতে দিত না।
—বুবু, আমি যহন থাকমু না তহন কইরেন। দেখমুও না, কষ্টও লাগবো না। আমি যতদিন আছি, আপনার কোনো কাজের গায়ে হাত দেওন লাগবো না।
— একটু না করলে যে অসুস্থ হয়ে যাবে রে।
— যাইবেন না। সকাল সকাল হাঁটতে যাইবেন। তাইলেই হইব।
লেখাপড়ায় খুব ভালো ছিল সীমা। আগ্রহও ছিল বেশ। আমরাও তাই যতটা পেরেছি সহযোগিতা করেছি, যাতে কাজের পাশাপাশি লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে। আবুল আর আয়শা ওর ছোটো দুই ভাইবোন। বাবা-মা সহ ভাইবোনকে নিয়ে সীমার অনেক স্বপ্ন ছিল। নিজে যতটুকু সম্ভব লেখাপড়া চালিয়ে যাবে, কিন্তু আবুল আর আয়েশাকে শেষ পর্যন্ত পড়াবে। যাতে শেষ জীবনে বাবা-মাকে কষ্ট করতে না হয়। আরও কত স্বপ্ন সীমার! সে স্বপ্ন শহুরে অভিজাত বাড়ির পিতলের টবে যত্নে বেড়ে ওঠা কোনো বাহারি ফুলের মতো ছিলো না; ছিলো শান্ত, নিবিড় পল্লিতে আপনি ফুটে থাকা মিষ্টি গন্ধের হিজল ফুলের মতো। আর আমার কাছেই জমা রাখতো ওর সেই নির্মল চাওয়াগুলো। কোনো ব্যস্ত সন্ধ্যায় রান্নার ফাঁকে উনুনের পাশে বসে, তিল তিল করে জমানো টাকা হিসেবের কালে, কোনো রোদেলা নবান্ন দিনের কাজের অবসরে দুপুরের ঝকঝকে আলোর মতো স্বপ্ন পূরণের দৃঢ়তার দ্যুতি দেখতাম ওর চোখে-মুখে। সে আভা বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়তো সমস্ত সত্তায়। বেড়ে যেত কাজের গতি। আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি একটা হাসি দিতো, যেন সুখের দিন খুব সন্নিকটে। আমি ওর কথা শুনেছি আর সাহস যুগিয়েছি, সব সময় পাশে থাকবার আশ্বাস দিয়েছি।
—বুঝছো ফুপু, লেখাপড়া শিইখ্খা যদি ছোডো খাডো একটা চাকরি যোগাড় করতে পারি, সবার আগে মার থাকার ঘরডা পাকা কইরা দিমু। লাকড়ি দিয়া রান্না করলে ধুঁয়ায় মার শ্বাস কষ্ট বাইড়া যায়। একটা গ্যাস সিলিন্ডার কিনতে পারলে মার আর কষ্ট হইব না। আবুল রে যদি মানুষ করতে পারি, তয় মার কষ্ট আর কয়দিন! তুমি কিন্তু আমারে দাদার কাছ থেইকা টাকা চাইয়া দিবা।
যদিও ওর ছোটোখাটো সব ইচ্ছেই আমরা পূরণের চেষ্টা করতাম, তবু সবার জীবনেই নিজস্ব কিছু ইচ্ছে থাকে, স্বপ্ন থাকে, বাসনা থাকে যা হয়তো অন্য কারও পক্ষেই পুরোপুরি পূরণ করা সম্ভব হয় না। সীমার মাথায় হাত রেখে বললাম, আচ্ছা, টাকা চেয়ে দেব আব্বার কাছ থেকে।
—শুধু আচ্ছা কইয়া পার পাইবা না। তোমারও কিন্তু আমারে সাহায্য করতে হইব। তুমি একলা করলে হইব না। তুমি আর তোমার জামাই দুইজনে আলাদা আলাদা টাকা দিবা।
হেসে দিই আমি,
— আমি জামাই পাব কোথায় রে। ততদিনে তোকেই শ্বশুর বাড়ি পাঠিয়ে দেব, পাগলি।
—কী যে কও ফুপু। বিয়া বহুত দূরের কথা। আব্বা-মার সব ব্যবস্থা কইরা না দিয়া অমন কথা চিন্তায়ও আনমু না।
আমি শুনতাম আর ওর চোখের গভীরে তাকাতাম। কী কঠিন প্রত্যয়! নির্ভেজাল চাওয়া বাবা-মায়ের জন্য। অথচ সর্বস্ব ত্যাগে মানুষ করা কত সন্তানের কাছে তাদের বাবা-মায়েরা কত অবহেলায় থাকেন। কখনো বা সন্তানদের সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্যটুকুও হয় না। সে চিন্তা করলে, সীমার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। দিনের আলোর চেয়ে ভোরের আধফোটা আলোয় সাদা টগর যেমন বেশি সুন্দর, তেমনি পৃথিবীর সব সুবিধা-বঞ্চিত, অল্প আলোয় বেড়ে ওঠা সীমার একদম ভেতর থেকে বাবা -মা, ভাইবোনের জন্য চাওয়াগুলোও ছিল শুভ্র, সুন্দর, নির্ভেজাল। কোন ভণিতা নেই তাতে, নেই কোনো স্বার্থপরতা। গভীর জীবনবোধসম্পন্ন, সহজ-সরল অথচ বুদ্ধিদীপ্ত মেয়েটার পরোপকারী সুন্দর মনটার জন্য অনেক ভালোবাসতাম ওকে।
২—
সব মানুষের বুকের ভেতর একটা আকাশ থাকে। সেই আকাশে থাকা রামধনুটা নিজ ইচ্ছেতেই রং ছড়ায় জীবনের কোণে কোণে, আবার কখনো কখনো সে রং মুছে নেয়, হয়তোবা নিজের অনিচ্ছায়। মায়ের হঠাৎ মৃত্যু পালটে দেয় সীমার জীবনের গতিপথ। এক বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে বিছানায় পড়ে থাকা মায়ের নিথর দেহটা দেখে কিছুতেই যেন সীমা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। পাগলের মতো ছুটাছুটি করছিল এদিক সেদিক। ‘মা ’ ‘মা’ বলে সীমার গগনবিদারী চিৎকার যেন পৌঁছে যাচ্ছিল ওর একান্ত আকাশের সেই রামধনুটার কাছে। আর রামধনুটাও যেন বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছিল ওর কষ্টে। এক সময় মায়ের নিঃসাড় বুকের ওপর পড়ে রইল সীমার সংজ্ঞাহীন দেহ আর তার অজস্র না ফোটা কলির মতো স্বপ্নগুলো।
মায়ের অসময়োচিত হঠাৎ মৃত্যুর আকস্মিকতায় আর সাজানো স্বপ্নগুলো এক নিমিষে খান খান হয়ে যাওয়ায় মানসিকভাবে খানিকটা এলোমেলো হয়ে গেল সীমা। প্রায়ই মায়ের কবরের কাছে নীরবে বসে থাকে। মাঝে মধ্যে বিড়বিড় করে একা একা কথা বলে মায়ের সাথে। সীমা যেমন আমাদের অকুণ্ঠ ভালোবাসা দিয়েছে, আমার বাবা-মাও তেমনি অকৃপণ ছিলেন ওদের পরিবারের সবার ব্যাপারে। কাজের অবসরে সীমা আমার কাছে কাছেই থাকত। আমি রাত জেগে পড়তাম। ও বসে থাকত আমার পাশে, আমি না ঘুমানো অবধি। নিজের পড়া তৈরি করত আর গল্প করত আমার সাথে। বেশিরভাগ গল্পই ছিল ওর মাকে ঘিরে, ভাইবোনের মঙ্গল নিয়ে।
—ফুপু, জীবন এমন ক্যান! মা আর কয়ডা দিন বাঁচলে দুইন্নার কী ক্ষতি হইতো, কওতো! ফুলের আর মাইনষের জীবন মনে অয় একই রহম। এই গন্ধ বিলায়, একটু পরেই আবার টুপ কইরা ঝইরা পড়ে। মায় একটু সুখের মুখ দ্যাখতে পারল না। কিচ্ছু করতে পারলাম না মার জন্য।
—জীবন এমনই সীমা। আমরা কেউই জানি না, একটু পরে কী হবে। আল্লাহ তায়ালা যখন যে অবস্থায় রাখেন, ধৈর্য ধরে তখন সেই অবস্থাকেই মেনে নিতে হয়। তাছাড়া তুই এমন করলে আবুল, আয়েশা ওরা তো আরো ভেঙে পড়বে।
—আবুলের মুখটার দিকে চাইতে পারি না ফুপু। মায় মারা যাওয়ার পর একদম কতা কয় না। খালি মার কবরের কাছে গিয়া দাড়াইয়া থাহে। আর চোখ দিয়া টপটপ কইরা পানি পড়ে। আমাগো দুই বুইনের পরে আবুল হইসে। মার কত আদরের ছিল ও! আহারে!
বলতে বলতে বুক চেপে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে
—মা…
—তোর বাবার জন্য, আবুল, আয়েশার জন্য তোকে সুস্থ থাকতে হবে সীমা। লেখাপড়া চালিয়ে যেতে হবে।
—ফুপু, তোমার যদি বিয়া হইয়া যায়, আমি তয় কার কাছে কমু আমার মনের কথা?
—আমার কাছেই বলবি। যখন ইচ্ছে ফোন করবি। তাছাড়া তোকে শ্বশুরবাড়ি না পাঠিয়ে আমি কোথাও যাব না রে।
দুষ্টুমি করে বললাম , তোর আগে আমি শ্বশুরবাড়ি চলে গেলে বিয়েতে তোকে সাজিয়ে দেবে কে, শুনি! এত সুন্দর করে সাজিয়ে দেবো, দেখবি, তোর বর চোখ ফেরাতে পারবে না। আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সীমা। কোনো কথা নেই। ক্রমশ শুকিয়ে যাওয়া মরা নদীর মতো সে দৃষ্টি। মাথায় হাত রাখতেই আবার ওর হু হু কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে চারপাশ।
বড়ো বোনরা যেন মায়েরই পরিপূরক। ছোটো ভাইবোনদের জন্য তাদের বুকেও মায়ের মতোই একটা ভালোবাসার নদী প্রবহমান। মায়ের মৃত্যুর পরে সংসারের ভার পুরোপুরি নিজের কাঁধে নিয়ে নেয় সীমা। আগলে রাখে বাবাসহ ছোটো ভাইবোনদের। কিন্তু ওর বাবার জন্য পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনদের শুরু হয় উপচে পড়া দরদ। কীভাবে সে একা কাটাবে ভবিষ্যতের দিনগুলো! অথচ ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভালোই কেটে যাচ্ছিল তার দিন। সবার উসকানির মুখে এবং নিজের ইচ্ছেতে বা অনিচ্ছাতে হোক, এক সময় দ্বিতীয় বিয়ে করে সীমার বাবা। নতুন বউকে পাশে পেয়ে খলখলিয়ে ওঠে তার জীবন। কিন্তু মাকে হারিয়ে সীমাদের জীবন হয়ে ওঠে বিরান মরুভূমি। খেয়ে না খেয়ে তিল তিল করে গড়ে তোলা মায়ের সংসারে অন্যের আধিপত্য মেনে নিতে সন্তানদের কষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বাবার দ্বিতীয় বিয়ে সন্তানদের প্রতি তার ভালোবাসায় এতটুকু কমতি ঘটায় না। হয়তো বাবার জন্য সন্তানদের ভালোবাসাও তাতে ফুরিয়ে যায়না । মানুষ অনেক সময় পরিস্থিতির স্বীকার হয়। হয়তো ওরাও তাই ভেবেছে। সীমা খুব বুদ্ধিমতী। ভেতরের অভিমান লুকিয়ে রেখে বাবার মুখ চেয়ে ওরা মেনে নিতে চেষ্টা করে নতুন মাকে। কিন্তু কথায় আছে না—সৎ মাও একটা মা, আর ডিম ভাজাও একটা তরকারি। বছর ঘুরতেই সীমার বাবা নতুন বউয়ের সন্তানের বাবা হয়। আর সৎ মায়ের কাছে ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে সীমারা কভাইবোন। ওদের জীবনে নেমে আসে দুর্যোগ। ওর বাবা না চাইলেও পরিস্থিতি এমন হয় যে একে একে সবাই বাড়ি-ছাড়া হয়। ওর ছোটো ভাই আবুলকে ভর্তি করে দেওয়া হলো কওমি মাদ্রাসার এতিমখানায়। ছোটো বোন গার্মেন্টসে চাকরি নিয়ে গ্রাম ছাড়া হলো। সীমার আকাশটা একেবারে শূন্য হয়ে গেল। গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে যাওয়া সে আকাশে সাদা বলাকারা আর ওড়ে না, সান্ধ্য পাখিরা আর কিচিরমিচির করে না, সে আকাশের গা থেকে কে যেন মুছে নিয়েছে সবটুকু জ্যোৎস্না।
৩—
চোখের সামনে তরতর করে বড়ো হয়ে গেল মেয়েটা। আব্বা মা প্রায়ই বলতেন সীমার একটা ভালো বিয়ে হলে তারা নিশ্চিন্ত হন। মেয়েটার মা নেই। কিন্তু সীমাকে রাজি করানো যাচ্ছিল না। মা অনেকদিন বুঝিয়েছে। আমি যখনই বোঝাতে চাইতাম, শুনতে চাইতো না। ওর ধারণা বড় হয়ে গেছে বলে ওকে আর আমরা কাজে রাখতে চাইছি না। তাই হয়তো বিয়ে দিয়ে দিতে চাইছেন আব্বা-মা।
—আমাগো গরিব মানুষের কপাল। বিয়ার পরে নতুন যন্ত্রণা শুরু হইব। আমার বিয়া লাগব না বুবু। আপনাগো কাছেই জীবন পার করমু। ও ফুপু, পালতে পারবা না আমারে? দাদা-বু না পারলে শ্বশুরবাড়ি যাওনের সময় তুমি তোমার লগে লইয়া যাইও আমারে!
মায়ের মৃত্যুজনিত মানসিক ধকল কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই সীমার জীবনের দ্বিতীয় বড়ো মানসিক আঘাতটা আসে ওর আপন বোনের কাছ থেকে। বিয়ের ফুল ফোটার তিন দিনের মাথায় ওর ছোটো বোন সীমার স্বামীর হাত ধরে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়।
সীমার এই মানসিক ক্ষতি পূরণের জন্য মা’র সাথে পরমর্শ করে আব্বা মাস ছয়েকের মধ্যে আবার সীমার বিয়ে ঠিক করেন। ছেলেদের ছোটো সংসার। অবস্থাসম্পন্ন। শ্বশুর বেঁচে নেই। সৎ ভাইসহ দুই ভাই। ছেলের নিজের একটা দোকান আছে। ভালোই রোজগার হয়। ক্লাস নাইন পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে। কিছু জায়গা-জমিও আছে। এখানে সম্বন্ধ হলে সীমা ভালোই থাকবে।
সবার সম্মতিক্রমে একটা শুক্রবার দেখে বিয়ের দিন তারিখ ঠিক হয়। আমিই সীমাকে সাজিয়ে দিই। বিয়ের শাড়ি শ্বশুরবাড়ি থেকে দিলেও আমি একটা শাড়ি কিনি ওর জন্য, রুপালি জরির কাজ করা লাল টকটকে। মাথার মাঝ বরাবর সিঁথি কেটে লম্বা বেণি করে তাতে বেলিফুল জড়িয়ে দিই। চোখে কাজল টেনে, কপালে লাল টিপ দিয়ে, ঠোঁট এঁকে তাতে লাল লিপিস্টিক লাগিয়ে দিই। বাস, এটুকু সাজেই অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল ওকে। আঁচলটা টেনে মাথায় দেওয়ার পর মনে হলো যেন একটা পরি বসে আছে আমার সামনে। চোখ ফেরাতে পারছিলাম না।
—সীমা দ্যাখ্ কত্তসুন্দর লাগছে তোকে। তোকে দেওয়া কথা রেখেছি কিন্তু! আর অমনি আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্না।
—ফুপু, দোয়া কইরো আমার লাইগা। তোমরা ছাড়া আমাগো আর কে আছে! দাদা-বু’র দিকে খেয়াল রাইখো।
—তুই কি চিরদিনের মত যাস্ নাকি! বোকা কোথাকার! আর বুঝি আসবি না শ্বশুরবাড়ি থেকে!
—কার কাছে আসুম!
—আমাদের কাছে আসবি।
—দাদারে কইয়ো আবুলের একটু খোঁজ খবর নিতে। তোমরা ছাড়া অর আর কেউ থাকল না।
বুকের ভেতর খুব চাপা কষ্ট হচ্ছিল আমারও। কাজের অবসরে আমার একমাত্র সঙ্গী ছিল সীমা। ও আমার চেয়ে কয়েক বছরের ছোট হলেও এত বুদ্ধিমতী ছিল যে ওর সাথে অনেক কথাই শেয়ার করা যেত। কাপড়চোপড়েও ছিল খুব পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি। সবকিছুতেই ছিল ভীষণ গোছানো। ভালো লাগত ওর পরিমিতিবোধ।
সন্ধ্যায় সীমাকে নিয়ে গেল ওর শ্বশুরবাড়িতে। ভীষণ শূন্য লাগছে। অদূরে দাঁড়িয়ে কাঁদছে সীমার ভাই আবুল। ওর মা বেঁচে থাকলে হয়তো অনেক আনন্দ করেই বোনকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাত। সত্যিই আজ ছেলেটা বড়ো একা হয়ে গেল। মা’র চোখে পানি। আব্বাও মুখ ভার করে বসে আছেন। সীমা বলতে গেলে বড়ো হয়েছে আমাদের কাছেই । রাতের খাবার খাওয়ার পরে পানের বাটা গোছাতে গিয়ে আব্বার চোখ ছলছল হয়ে ওঠে। সত্যিই মেয়েটার অনেক মায়া ছিল আমাদের জন্য। বিয়ের দিনের এত কাজের ভিড়েও আব্বার পানের বাটাটা সুন্দর করে গুছিয়ে রাখতে ভুল করেনি। যেখানে হাত দিই সেখানেই সীমার হাতের ছোঁয়া। পরিপাটি করে সবার আলমারি গুছিয়ে রেখেছে। আব্বা-মা’র আলমারিতে তাদের ঘরে পরার কাপড়, বাইরে পরার কাপড় সব আলাদা আলাদা করা। মেয়েটা জানত কী করে ভালোবাসা আদায় করে নিতে হয়। দিনে দিনে আমাদের আর সীমার মধ্যে তৈরি হয়েছে এক মায়ার সেতুবন্ধন। আসলে নিজের বুদ্ধিমত্তা আর ভালোবাসা দিয়ে সে নিজেই তৈরি করে নিয়েছে সেই আত্মিক বন্ধন। মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখা আমাদের পারিবারিক শিক্ষা। ধন, সম্পদের তারতম্যের বিভাজনে মানুষের মর্যাদা বিভাজ্য নয় আমাদের কাছে। সীমাকেও আমরা সেভাবেই দেখেছি।
প্রথম প্রথম কিছুদিন হাসিমুখেই শ্বশুরবাড়ি থেকে আসা যাওয়া করে সীমা। কারণ বিয়ের সময় ওদের দাবি অনুযায়ী পরিশোধ করা যৌতুকের রেশ তখনও ছিল। বিয়েতে বিশ হাজার টাকা ক্যাশসহ সংসারের প্রয়োজনীয় সবকিছু আব্বা এমনভাবে দিয়ে দেন যাতে ওদের একটা হাঁড়িও কিনতে না হয়। কিন্তু যৌতুকের সেই উত্তাপ বেশিদিন রইল না। কিছুদিনের মধ্যেই আবিষ্কৃত হলো সীমার বর নেশা করে, জুয়া খেলে। ‘অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকিয়ে যায়।’ জুয়াড়ু, নেশাগ্রস্ত স্বামী, সৎ শাশুড়ি আর সৎ দেবর নিয়ে অভাবের সংসার। যা কামাই করে, তার সবই নেশা আর জুয়ার আগুনে ভস্ম। সৎ শাশুড়ি আর অভাবের সংসারে হাঁড়ি থেকে নিজ হাতে খাবার বেড়ে খাওয়ার সুযোগ হয় না সীমার। সারাদিনের কাজ শেষে খাওয়ার জন্য শাশুড়ির ডাকের অপেক্ষায় থাকতে হয়। তার মর্জি হলে তবেই খাবার জোটে। সকালের খাবার দুপুরে, দুপুরের খাবার রাতে। মেপে একবারে ভাত দেন। তাতে পেট ভরলো তো ভরলো, না ভরলে আধপেটা খেয়েই থাকতে হতো। তারপর নেশার আর জুয়ার টাকার জোগান না হলে স্বামীর হাতে বেদম প্রহার তো আছেই। বাবার বাড়িতে এসেও এক বেলা খাওয়ার উপায় নেই। শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে তাই ভালোমন্দ দুমুঠো আমাদের বাড়িতেই খেত। দুদিন থেকে চলে যেত। আব্বা তার সাধ্যমতো চেষ্টা করতেন সীমার আরেকটু বেশি সুখের জন্য। কিন্তু আগুনে পড়লে পোড়াই যে পরিণতি! নগদ টাকা দিয়ে কতদিন চালিয়ে রাখা যায়। নেশা করার জন্য সীমার বর শেষ পর্যন্ত দোকানটাও বিক্রি করে দিলো । আর তার জেরে সীমার ওপর বেড়ে গেল শাশুড়ির অত্যাচার। খাবারের পরিবর্তে জুটতে লাগলো গালি-গালাজ, প্রহার।
ক্রমবর্ধমান তিক্ততার এক পর্যায়ে অবস্থা এমন হলো যে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে সীমা একবার চলে আসে, ছেলে-মেয়ের মুখ চেয়ে আবার চলে যায়। স্বামী যদি ভালো হয়ে যায়, সেই আশায়। বাবার নতুন সংসারেও নেই পর্যাপ্ত কামাই। বাবার বাড়িতেও তাই থাকবার উপায় নেই। বাচ্চারা ছোটো, তাই গার্মেন্টসেও কাজ করা হয় না। ওদের কার কাছে রেখে কাজ করবে? তাই সমস্ত অত্যাচার, নির্যাতন মেনে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতেই মুখ গুজে পড়ে থাকে।
৪—
শ্বশুরবাড়ি থেকে একদিন সীমার অসুস্থতার খবর আসে। সীমার বাবা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে আব্বার কাছে। জানায় সীমার অসুস্থতার কথা। আব্বার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ছুটে যায় ওর শ্বশুরবাড়ি, মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে সীমাকে। কিন্তু এ কোন সীমা! মানসিক ভারসাম্যহীন সীমা চিনতে পারে না কাউকে, চোখে এলোমেলো শূন্য দৃষ্টি। মনের কষ্ট আর প্রচণ্ড অপুষ্টিতে কোনোরকম নিশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছে। বাচ্চাগুলোর মতো নিজেও হাড্ডিসার, তেলহীন উস্কো-খুস্কো চুল, চোখ কোটরাগত। দুই সন্তানের মা হতে গিয়ে চরম অপুষ্টির স্বীকার হয়েছে সীমা। তিনবেলা খাবারই জোটেনি, গর্ভকালীন পুষ্টিকর খাবার তো দূরের কথা। দিনের পর দিন অভুক্ত থাকায় আর শারীরিক অত্যাচারে সীমার জীবনপ্রদীপ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যেন তা ঝড়ো-বাতাসের মুখে অল্প তেলের পোড়া সলতের এলোমেলো শেষ আলো, দপ করে নিভে যাবে যখন তখন।
সৎ মা নিজেই মানুষের বাড়িতে কাজ করে নিজের সংসার চালায়। সীমা আর তার বাচ্চাদুটোসহ সংসারে এখন সদস্য সংখ্যা ছয়জন। তবু অন্তত শ্বশুরবাড়ির শারীরিক অত্যাচার না থাকায় তিন বেলা খেতে না পেলেও মাস খানেকের মধ্যে ক্রমান্বয়ে সীমার শরীরের উন্নতি হতে থাকে। একটু সুস্থ বোধ করলে সংসারের চরম দারিদ্রের কথা ভেবে বাচ্চাদেরকে বাবা এবং সৎ মায়ের কাছে রেখে সীমা ঢাকায় গার্মেন্টসে চাকরি নেয়। কিন্তু কঠিন অসুখের ধকল সামলে উঠতে না পারা শরীর নিয়ে চাকরি বেশিদিন করতে পারে না ও। একদিন প্রচণ্ড অসুস্থ অবস্থায় ঢাকায় আমার কাছে ওকে নিয়ে আসি। কিন্তু পুষ্টিকর খাবার আর পর্যাপ্ত বিশ্রাম সত্ত্বেও দিন দিন ওর শরীর যেন শুধু খারাপের দিকেই যেতে থাকে। ডাক্তার দেখাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাই। ডায়াগনসিস হয়, অ্যাডভান্সড স্টেজ এপিলেপ্সিতে আক্রান্ত সীমা। শরীরের ক্রমাবনতিতে এখন সারাক্ষণ ওর হাত কাঁপে। হাঁটতে খুব কষ্ট হয়, পা এলোমেলো হয়ে যায়। কথা জড়িয়ে যায়। মুখ থেকে লালা ঝরে। হয়তো আরও অনেক আগে থেকেই চিকিৎসা করানো দরকার ছিল। কে করাবে! ঠিকমতো দুবেলা খাবারই যেখানে জোটেনি, সেখানে চিকিৎসা তো অনেক দূরের কথা। একটু সুস্থ হলে ওর বাবা এসে সীমাকে গ্রামে নিয়ে যায়। ওষুধপত্র কিনে দিয়ে এবং সাথে কিছু নগদ টাকা দিয়ে ওকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিই।
সবার জীবনেই কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। উঁচু কিংবা নিচু—সমাজের সব স্তরের মানুষের জীবনের বাঁকে বাঁকেই থাকে নানান ঝুট-ঝামেলা, অসংগতি। চাইলেও সবসময় সবার জন্য সবকিছু করা সম্ভব হয় না। তারপরও সীমার প্রতি আমাদের সীমাহীন মায়া, কর্তব্যবোধ এবং আমার ওপর ওর অগাধ অধিকারবোধের কারণে সবসময় ওর জন্য আমি কিছু করার সাধ্যমতো চেষ্টা করি। কিন্তু চাকরি, সংসার সামলে দূর থেকে আমি আর কতটুকুই বা করতে পারি! আব্বা বেঁচে থাকলে হয়তো সীমার জীবনটা আরেকটু সহজ হতো, হয়তো আমাকে এতটা ভাবতে হতো না। মায়ের বয়স হয়েছে। তিনি এখন আমার কাছেই থাকেন। মা ফোনে সবসময়ই খোঁজ রাখেন সীমার। আমি নিয়মিত টাকা পাঠাই ওর খাওয়া আর চিকিৎসার জন্য। ওষুধপত্র খেয়ে দুদিন একটু ভালো থাকে, আবার অসুস্থ হয়ে যায়। দিনে দিনে ওর অসুস্থতা বেড়ে যেতে থাকে। এক সময় অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে হাত দিয়ে আর খেতে পারে না। খাবার পড়ে যায় হাত থেকে। কথা বলতে ভীষণ কষ্ট হয়। জিহ্বায় জড়িয়ে যায়। ওকে খাইয়ে দেওয়ার, গোসল করানোর দায়িত্বটুকু সস্নেহে ওর বাবাই নিজ কাঁধে তুলে নেয়। প্রাপ্তবয়স্কা কন্যার সেবা করার ক্ষেত্রে সব সীমাবদ্ধতার ঊর্ধে উঠেও তার চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। বাচ্চা দুটোও ছোটো। সীমার দেখভালসহ বাচ্চাদের যত্নও ওর বাবাই করে। সে নিজেও সুস্থ নয়। নিশ্বাস টেনে তুলতে পারে না। ওর মায়ের মতো সেও অ্যাজমার রুগি। কৃষি, গৃহস্থালি কিংবা বাইরের কাজ করার মতো শক্তি-সামর্থ্য তার আর নেই। সৎ মায়ের একার ঝিয়ের কাজে এতগুলো মানুষের সংসার আর চলতে চায় না। দুর্গতি যেন আর ওদের পিছু ছাড়ে না! তুমুল যুদ্ধ জীবনের সাথে! জীবনটা যেন, সহজে টেনে তোলা যায়না এমন এক কঠিন বোঝা! অভাব- অনটন, দুঃখ-কষ্টের সাগরে খাবি খেতে খেতে পার হতে থাকে একেকটি দিন, মাস, বছর।
৫—
সীমার ভাগ্যটা যেন এক অস্তমিত সূর্য, যে থাকে রাতের গহ্বরে, আলো দিতে জানে না। সীমার জীবনে আবারও আসে অসহনীয় আঘাত। চরম অপুষ্টি, অযত্নে প্রায়ই অসুস্থ থাকত ওর মেয়েটা। একে তো নিজে অসুস্থ, সেই অবস্থায় নিজের কোলের মধ্যেই একদিন মেয়েটা অ্যাকিউট নিউমোনিয়ায় মারা যায়। দুঃখ-কষ্ট, আঘাত, বেদনার অনুভূতিগুলো ধনী, গরিব নির্বিশেষে একইরকম। মায়ের কোনো জাত হয় না। মেয়ের লাশ কোলের মধ্যে নিয়ে বসে আছে সীমা। কান্নার শক্তি নেই। এপিলেপ্সির কারণে কথা বলতে পারে না। জিহ্বা জড়ানো কণ্ঠে মা মা বলে কয়েকটা চিৎকার দিয়ে থ’ হয়ে বসে আছে। কথা বলার শক্তিটুকু নেই। চোখ দিয়ে টপটপ করে গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা। বোবা কান্নার তুফান অনেক বেশি। নীরবে ভেঙে যায়। সে ঢেউ কেউ টের পায়না। ঘরের কোণের আম গাছটা ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু দেখেছে চির শয়ানের জন্যে মেয়েকে নিয়ে যাওয়া।
মেয়ের লাশের সাথে সাথে সেই যে সীমা ঘরের বাইরে বের হয়েছে, তারপর থেকে ওকে আর কেউ স্বেচ্ছায় ঘরে নিতে পারেনি। একের পর এক মানসিক আঘাতে মানসিক ভারসাম্যের সবটুকুই হারিয়ে গেছে ওর। এখন আমগাছটার তলায়ই ওর রাত আর দিনের বেশিরভাগ সময় কাটে। ঘরে নেয়ার চেষ্টা করলেই চিৎকার, চেচামেচি জুড়ে দেয়। শুধু ঝড় বাদলের সময়ে জোর করে কিংবা অনেক রাতে ঘুমিয়ে পড়লে ওর বাবা ওকে ঘরে নিতে পারে। ভোর না হতেই আবার ওখানে না যাওয়া অবধি চিৎকার করে। নিজের মনে কথা বলে। কখনো চুপচাপ থাকে। ক্ষুধা লাগলে হাউমাউ করে। বাবাকে ডাকে। একমাত্র ওর বাবার কথাই একটু শোনে। মেয়ের সাথে সাথে তার সময়েরও অনেকটাই এখন ওখানেই পার হয়। দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয় কারণ ছেড়ে রাখলে একা একা এদিক সেদিক চলে যায়।
সীমার অসুস্থতা বেড়ে যাবার সংবাদ পেয়ে গ্রামে যাবার জন্য মনটা ছটফট করে উঠল। আব্বার কবরটাও জিয়ারত করার আকুতি অনুভব করলাম। গ্রামের বাড়িতে এসে সীমার এই করুণ পরিণতি দেখতে হলো। মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছিল ভীষণ। জীবনের হিসেব বড্ড জটিল। ওর চিকিৎসাসহ খাবারের টাকা পাঠাতে কখনোই আমার ভুল কিংবা দেরি হয়নি। এটা ছাড়া আমার আর কী-ইবা করার ছিল! একদিন খুব সকালে সীমার বাবার ফোন এলো। সীমা খুব বেশি অসুস্থ। কেন জানিনা, এবার আমার মন অন্য সব কারণ ছাপিয়ে শুধু সীমাকে দেখতে যাবার জন্যই বেশি অস্থির হলো। কিছুদিন ধরে মাও আব্বার কবর জিয়ারত করতে গ্রামে যাবার জন্যে ছটফট করছিলেন। সীমার অসুখের খবরে ভীষণ উদ্বিগ্ন এবং আরও উতলা হলেন। তাঁকে নিয়ে সকালেই রওয়ানা হলাম ঢাকা থেকে। পৌঁছালাম বিকেল নাগাদ। গিয়ে যা দেখলাম তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আমাদের দেখেই সীমার বাবা বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ল, ‘আর তোমাগো টাকা পাঠাইতে হইব না। তোমাগো সীমা আর খাওন চায় না। ফুরাইয়া গেছে সীমা।’
শেষের দিকে একদম নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল সীমা। খেতেও চাইত না। এক সময় ক্ষুধা পেলে কান্নাকাটি করত। কিন্তু এখন আর খাবার চায়না। মা আর আমি অনেক ডাকাডাকি করার পর একবার শুধু চোখ তুলে তাকালো।
সীমাদের বাসা আমাদের বাসার লাগোয়া। ফজরের আজানের পরপরই ঘুম ভাঙল ওর বাবার চিৎকারে—সীমা, মাগো, মা! তুই কী চইলা গেলি আমাগো ছাইড়া! মা, মা, মাগো …
দৌড়ে গেলাম। সীমার নিস্তেজ নিথর শরীর সীমার বাবার বুকের মধ্যে। সীমা এবার সত্যিই চলে গেছে এই ক্ষুধার্ত পৃথিবীর অনাকাঙ্ক্ষিত অবহেলাকে ভ্রুকুটি করে। শূন্য হাতে এসে চলে গেছে শূন্য হাতে। চলে গেছে হাজার তারার মাঝে, আকাশের বুকে। যেখানে ক্ষুধা নেই, অবহেলা নেই, দারিদ্র নেই, মনভাঙার গল্প নেই।
আমাদের এ সময় বাড়িতে আসার কথা ছিল না। সীমা কি তবে আমাদের অপেক্ষায় ছিল! আমাদের কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে পৃথিবী থেকে যাবে না বলে, তার প্রিয় বুবুকে না দেখে চোখ বন্ধ করবে না বলে! মা কাঁদছে, আমি ভেঙে যাচ্ছি। আব্বা বেঁচে থাকলে আজ তাঁর ভীষণ কষ্ট হতো।
উঠোনে খাটিয়ায় সীমার লাশ। খাটিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ছেলে তামিম। ঘরের দাওয়ায় বসা নানার মুখের দিকে তাকায় একবার, মায়ের লাশের দিকে তাকায় একবার। কাঁদে না, কিছু বলেও না। শুধু তাকিয়ে থাকে। খাটিয়া কাঁধে নিয়ে দাফনের উদ্দেশে যখন যাত্রা শুরু হল, তখন হঠাৎ ‘মা, মাগো’ বলে চিৎকার দিয়ে দৌঁড়ে যায় সবার পেছন পেছন। যে ‘মা’ ডাকের জন্য এতদিন সীমার তৃষিত মাতৃত্ব উদগ্রীব হয়ে ছিল, আজ সেই ডাক নিশ্চয়ই পৌঁছে যাবে তার কাছে। সব আক্ষেপ শেষ করে এবার পরম শান্তিতে ঘুমাবে সে! উদ্বেল তুফানের সীমা আজ এক শুকনো নদী হয়ে ঘুমিয়ে গেছে মাটির কোলে। জীবনের সুরে সুর মেলাতে না পারা এক আশাহত আত্মার পরিসমাপ্তি ঘটেছে।
ঢাকায় চলে আসার সময় তামিমকে দেখলাম, ছোট্ট হাতে মায়ের কবরের শুকনো ঘাস পরিষ্কার করছে। আজ সীমার জীবনের বুঝি এটুকুই সার্থকতা।